আমাদের ভিরাল্লার ঈদ– জুবাইদা নূর খান

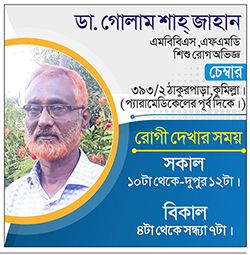
আমার বুবু অর্থাৎ আমার দাদি ছিলেন জাঁদরেল ধরনের মহিলা। চোখগুলো বেশ বড় আর গোল গোল। সোনালি ফ্রেমের চশমাটাও ছিলো গোলাকার। তিনি তার পুত্র – কন্যা কিংবা নাতি- নাতনিদের নিকট সহজ ছিলেন না। সাধারণত দাদি- নানি বলতে যা বুঝায় অর্থাৎ নাতি- নাতনির জ্বালাতন সহ্য করা, তাদের আবদার মেটানো ইত্যাদি। আমরা আমাদের বুবুর মধ্যে ঐসকল গুণাবলীর একটাও দেখিনি। তারপরও আমরা বুবুকে খুবই ভালোবাসতাম। বুবু আমাদের কাছে ছিলেন দুর্বোধ্য, কেমন একটা রহস্যময়ী! কেনো বুবুর কথা লিখছি, তাইতো? শৈশবের কোরবানির ঈদের কথা লিখতে গেলে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই বুবুর কথা চলে আসে। শৈশবে ‘ঈদ উল আযহার’ চাইতে ‘কোরবানির ঈদ ‘ এই শব্দটিই আমাদের মধ্যে বেশি প্রচলিত ছিলো।
যাহোক, কোরবানির ঈদ সমাগত। বুবুর জীবদ্দশায় তাঁর পুত্র, নাতি- নাতনিরা কেউ তাঁকে ছেড়ে শহরে ঈদ উদযাপনের কথা চিন্তাও করতে পারতো না। স্কুল ছুটি হলে ঈদের ২/৩ দিন পূর্বে আমাদের বাপ- চাচারা একে একে যার যার পরিবার নিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে যেতেন। আমাদের সে কী খুশি! আম্মা অনেক গুলো ব্যাগে ৩/ ৪ দিনের কাপড়, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতেন। আর একটা ব্যাগে থাকতো বুবুর জন্য কেনা – পান, সুপুরি, জর্দা, আর চিকন পাড়ের সাদা শাড়ি। সকালে আমরা রওনা করবো, তো উত্তেজনায় আমাদের রাতে ঘুম ঠিক মতো হতোনা। উল্লেখ্য, আমরা কিন্তু কোরবানি ঈদে নতুন জামা পেতাম না। আমাদেরকে শিখানো হয়েছিল যে, কোরবানি ঈদ মানে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গরু – খাসি কোরবানি দেয়া, গরীর – দুঃখীর মুখে হাসি ফোটানো। আমরাও এ বিষয় নিয়ে কখনো আবদার করিনি। যাহোক, বাসে করে গ্রামের বাড়ি যেতে হবে। জানালার পাশে কে বসবে সেটা নিয়েও চলতো রীতিমতো প্রতিযোগিতা। তবে, এই প্রতিযোগিতায় শোচনীয়ভাবে আমারই হার হতো। তো বাস ছাড়ার পর আমাদের সময় যেনো আর ফুরায়ইনা। একটু পর পর আমরা বোনেরা আব্বাকে জিজ্ঞেস করতাম, “আব্বা, আর কত দূর?” আম্মা রাগী মানুষ। রাগ দেখিয়ে বলতেন, “চুপ করে বসে থাকো। বাড়ি আসলে সবাই একসাথেই নামবো।” আব্বা মুচকি হেসে বলতেন, “এই তো, মা! আর ৪৫ মিনিট, আর আধ ঘন্টা;” ইত্যাদি ইত্যাদি। আর আমরা বোনেরা ঘড়ির কাঁটার উপর চরম বিরক্ত হতাম। ড্রাইভারের উপরও আমাদের অসন্তোষের সীমা ছিলোনা। বেটা একটা ফাজিল! ইচ্ছা করেই আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে – আমরা নিজেদের মধ্যে এভাবেই আমাদের অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করতাম। আমাদের গ্রামের বাড়ি ভিরাল্লা। আমাদের স্টেশনের কাছাকাছি আসতেই শোনা যেতো, ” যারা ভিরাল্লা নামবেন, রেডি থাকেন।” আমাদের আনন্দ তখন আর কে দেখে! স্টেশনে গাড়ি থামতেই আমরা হুড়মুড় করে নামার চেষ্টা করতাম। কী এক আনন্দ! অবশেষে আমরা গ্রামে পৌঁছেছি। শহরের চার দেয়ালে বন্দী আমাদের জীবন। স্কুল থেকে বাসা আর বাসা থেকে স্কুল। এই ছিলো আমাদের একঘেয়েমীপূর্ণ দিনলিপি।
সুতরাং আগামী ৩/৪ দিন আমাদের এই গৎবাঁধা জীবন যাপনে বৈচিত্র্যের পালক যুক্ত হবে এই আনন্দে আমরা বিভোর থাকতাম। একটু হেঁটে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে আমরা এক দৌড়ে বুবুর কাছে আগে যেতাম এবং কদমবুসি করতাম। পর্যায়ক্রমে বাড়ির অন্যান্য মুরুব্বিদেরকে। বাইরের কাপড় বদল করে বাড়ির চাচাতো ভাই – বোনদের নিয়ে বাড়ির আশপাশ ঘুরে দেখতাম। আমাদের বাড়ির ঠিক পেছনে একটা বিশাল বাঁশঝাড় ছিলো। ওটার দিকে তাকালে দিনের বেলাতেও কেমন অস্বস্তি বোধ হতো। কিন্তু গ্রামে বাস করা আমার চাচাতো ভাই বোনদের উৎসাহে বাঁশঝাড় পেরিয়ে আমরা হিন্দু পাড়ার দিকে যেতাম। বাড়িগুলোর সামনে অর্থাৎ উঠোনগুলো কী পরিষ্কার ছিলো! তুলসী বেদিতে রক্তজবা আর শ্বেত শুভ্র জুঁই – টগর দেখে আমার শিশুমনও এক অদ্ভুত ভালো লাগায় আবিষ্ট হতো। অপরদিকে, বাড়ির মুরুব্বিরা অর্থাৎ আমাদের বাপ-চাচারা তখন মিটিং করছেন। কতো টাকায় এবার কোরবানির গরু ও খাসি কেনা হবে। খান পরিবারের কোরবানি। আর্থিক অবস্থা কেমন সেটা বিবেচ্য নয়। বড় আর দামী গরু না হলে মানুষের কাছে মুখ থাকবেনা। এইরকম চিন্তা ধারা নিয়ে তাঁরা কোরবানির জন্য যৌথ বাজেট ঠিক করতেন। এরপর সকলের টাকা একত্রিত করে বাড়ির পুরুষ সদস্যরা দুপুরে খাওয়াদাওয়া সমাপ্ত করে গরুর হাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিতেন। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে প্রায় রাত। গলায়, শিংয়ে বিভিন্ন রংয়ের কাগজের তৈরি ফুলের মালা পরানো কোরবানির গরু যখন আমাদের আঙ্গিনায় উপস্থিত হতো,তখন সে কী হইচই! টর্চের আলো ফেলে কোরবানির উদ্দেশ্যে সদ্য ক্রয়কৃত গরু নিয়ে বিজ্ঞজনের আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু হতো। গরুটিতে কতটুকু মাংস হতে পারে; দামে ঠকে গেলো নাকি জিতা হলো ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা অতশত বুঝতামনা। তাছাড়া এতো ছোট বয়সে লাভ – লোকসান বুঝবার কথাও না। যাই হোক, সবাই চলে যাওয়ার পর গরুটাকে গোয়ালঘরে বেঁধে ভাতের মাড়, খড় খাওয়ানো হতো। ঈদের দিন খুব সকালে কোরবানির গরুটিকে গোসল করানো হতো। আব্বা-চাচা, চাচাতো ভাইয়েরা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে ঈদের জামাতের উদ্দেশ্যে রওনা দিতেন। তার আগে অবশ্য সবাই সেমাই-মুড়ি নাস্তা হিসেবে খেতেন। অন্যদিকে আমাদের মা-চাচীরা রান্নার বিভিন্ন উপকরণ জোগাড় করতে কাক ডাকা ভোর থেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। কোরবানির রান্নার জন্য প্রচুর মশলার ব্যবস্থা করতে হতো; তখন তো আর ব্লেন্ডার জাতীয় মেশিন ছিলোনা ; প্রচুর পেঁয়াজ – রসুন কাটতে হতো। কিছু কাজ অবশ্য কোরবানির আগের রাতেই গুছিয়ে রাখা হতো। মা-চাচীরা নাকের পানি, চোখের পানি এক করে পেঁয়াজ- রসুন কাটতে থাকতেন। তবে, যা ই করতেন সব কিছু বুবু অর্থাৎ আমার দাদিকে দেখিয়ে করতে হতো। বুবু নিজে কিছু করতেননা। কেবল নির্দেশনা দিতেন। মা-চাচীরা ছিলেন তাঁর আজ্ঞাবহ।
জামাত শেষে সবাই যখন বাড়ি ফিরতেন তখন সবার মধ্যে সে কী উত্তেজনা! বিশাল রাম দা হাতে হুজুরের পিছনে পিছনে ছোটখাটো একটা বহর। সেই সময়টায় হুজুর যেনো যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান সেনাপতি আর অন্যরা সাধারণ সৈনিক! সেই সময়গুলোতে অন্য বাড়ির ছেলেরাও কোরবানিতে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা করতো। কারণ তখনকার সামাজিক বন্ধন গুলো ছিলো অনেক মজবুত। সকলে সকলের কাজে আনন্দের সহিত ঝাঁপিয়ে পড়তো।
কোরবানির পর আমার বাপ- চাচারা বাড়ির উঠানে হাতলওয়ালা চেয়ারে বসতেন। ওনারা মাংস কাটায় হাত দিতেননা। এই কাজের জন্য পূর্ব থেকেই লোক ঠিক করা থাকতো। ৮/১০ জন লোক বাঁশের চাটাই বিছিয়ে মাংস কাটার কাজে বসে যেতেন। প্রথমে গরুর কলিজাটা বের করে ভেতর বাড়িতে পাঠানো হতো। মা- চাচীরা তাড়াতাড়ি সেটা রান্নার ব্যবস্থা করতেন। সাথে রান্না হতো সুগন্ধি চালের পোলাও। রান্নার ফাঁকে ফাঁকে বাপ- চাচাদের জন্য ঘন দুধের চা পাঠানো হতো। চা পানের ফাঁকে ফাঁকে ওনারা বাজখাঁই গলায় দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার ঝড় তুলতেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। উনারা কতো কী জানেন! যে বছর আমাদের কোরবানির গরুটা চার হাজার টাকায় কেনা হয়েছিলো, সেটা ছিলো আমাদের গ্রামের সবচেয়ে দামী গরু!
তালে তালে মাংস কাটা চলতো; সবশেষে হাড়গোড় প্রক্রিয়া করা হতো। এরই মধ্যে আমাদের বাচ্চাদের ডাক পড়তো। গ্রামে যে ঘরে খাওয়া দাওয়া হয় সেটাকে ‘বাইন্দর’ বলে। আমরা সেখানে পিড়ি পেতে গোল হয়ে বসতাম; মা-চাচীদের কেউ একজন খাবার বেড়ে দেওয়ার কাজটা করতেন। আমরা গরম গরম পোলাও আর কলিজা ভুনা খেতাম অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে। খাওয়া দাওয়ার পর সবাই দৌড়ে পুকুর পাড় অথবা বাড়ির আশেপাশে বিভিন্ন ধরনের খেলা খেলতাম। সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে মাংস কাটাকাটি শেষ হতো। চামড়া এতিমখানায় দিয়ে দেয়া হতো। এরই মধ্যে গ্রামের দরিদ্ররা আসতো গোস্ত নিতে। দরিদ্রদের ভাগ সুষম বণ্টন হতো। আর আত্মীয়-স্বজনের ভাগও কিভাবে, কার মাধ্যমে পৌঁছানো হবে তা আগে থেকেই ঠিক করা থাকতো। ফুপুর বাড়ি এবং আমাদের বিবাহিত জ্যাঠাতো- চাচাতো কিংবা ফুপাতো বোনদের যাদের শ্বশুর বাড়ি আমাদের গ্রামের কাছাকাছি সেইসব বাড়িতে বিভিন্ন লোক মারফত কোরবানির গোস্ত পাঠানো হতো। তাঁদের বাড়ি থেকেও আমাদের জন্য দেয়া হতো। এরপর আমাদের নিজেদের খাবারের জন্য গোস্ত ভিতর বাড়িতে পাঠানো হতো। আমাদের যেহেতু সদস্য সংখ্যা বেশি তাই লাকড়ির চুলায় বিশাল হাড়িতে একসাথে অনেক গোস্ত বসানো হতো। বুবুর পরামর্শে মা- চাচীরা হাড়িতে পরিমাণমতো তেল-মশলা দিতেন। উনাদের পক্ষে নাড়ানাড়ির কাজটা কঠিন ছিলো বলে পুরুষ সদস্যরা সেটা করতেন। বুবু চেয়ারে বসে সবকিছু ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কিনা তা দেখতেন। বুবুর সামনে তাঁর ছেলে- বউরা যেনো এক একটা ভেজা বিড়াল! এমন মা ভক্তি সত্যিই বিরল! রান্না শেষ হতে হতে রাত গভীর হতো। আমাদের বাচ্চাদের চোখ তখন ঢুলুঢুলু। কেউ কেউ আবার হাত-পা ছড়িয়ে গভীর ঘুমে অচেতন। আর এই সুযোগে গ্রামীন মশারা অনায়াসে তাদের রক্ত পান করে ফুলে ফেঁপে উঠছে। এক সময় আমাদের মা- চাচীরা টেনে হিঁচড়ে আমাদেরকে কোরবানির গোস্ত ভক্ষণের জন্য বসাতেন। বাচ্চাদের কেউ কেউ চিৎকার করে কান্নাকাটি জুড়ে দিতো। ঘুম থেকে উঠে খাবার খেতে তারা নারাজ। মা- চাচীরা বলতেন, কোরবানির দিন মাংস না খেলে আল্লাহ গুনাহ দিবেন। আমরা চোখ কচলাতে কচলাতে মাংসের টুকরো গিলতাম। তারপর কোনোমতে খেয়ে আবার ঘুম। এভাবেই শেষ হতো আমাদের শৈশবের কোরবানির প্রথম দিন।
লেখক:সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ।

