সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর সংবাদ
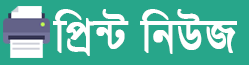
সাংবাদিকতার মানের জন্য হুমকি
বাহার উদ্দিন খান।।
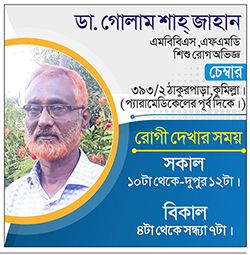
সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর সংবাদ আজকের সাংবাদিকতার মানের জন্য এক বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান বিশ্বে সোশ্যাল মিডিয়া কেবল মতপ্রকাশ বা বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং সংবাদ প্রচারের অন্যতম প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে। যেকোনো দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা সামাজিক ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ মুহূর্তের মধ্যেই ছবি ও ভিডিও ফেসবুক, এক্স বা টিকটকে ছড়িয়ে দেন। এর ফলে সংবাদ প্রচার দ্রুত হয়, কিন্তু একই সঙ্গে এক গভীর সংকট তৈরি হয় সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের মতো দেশসহ বিশ্বের বহু জায়গায় দেখা যায়, সংবাদপত্র বা টেলিভিশন গণমাধ্যম সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া কোনো ছবি বা তথ্য যাচাই না করেই প্রচার করছে। এর ফলে সংবাদমাধ্যমের মান প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে, বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে এবং সমাজে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ছে।
প্রচলিত সাংবাদিকতার ভিত্তি হলো নির্ভরযোগ্য তথ্য, সত্য উদঘাটন ও দায়িত্বশীলতা। সাংবাদিকতা কখনো
শুধু দ্রুত সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার নাম নয়, বরং জনগণকে সঠিক তথ্য জানানো এবং প্রতিটি ঘটনার সত্য ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করার একটি প্রক্রিয়া। অথচ সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর সংবাদ এই দায়িত্বশীলতাকে
দুর্বল করে দিচ্ছে। অনেক সংবাদকর্মী সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো ছবি বা পোস্ট দেখেই সেটিকে খবর হিসেবে ব্যবহার করছেন। কিন্তু পোস্টের উৎস কোথায়, তথ্যটি সত্য নাকি গুজব, ছবিটি আসল নাকি ভুয়া,এসব যাচাই করার মতো সময় নিচ্ছেন না। ফলস্বরূপ ভুয়া সংবাদ ছড়িয়ে পড়ছে, গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং পাঠক সমাজ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ছে।
বাংলাদেশে একাধিক ঘটনা এই সমস্যার চিত্র স্পষ্ট করেছে। কক্সবাজারে এক ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে
একটি ছবি কয়েক বছর আগে ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছিল। ছবিটি আসলে অন্য একটি ঘটনার হলেও বেশ কিছু পত্রিকা যাচাই না করেই সেটি ব্যবহার করেছিল। পরে প্রমাণিত হয় ছবিটি বহু বছর আগের। আরেকটি বড় ঘটনা হলো ভোলার বোরহানউদ্দিনে এক তরুণের ফেসবুক আইডি হ্যাক করে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ ছড়ানো। সংবাদ যাচাই না করেই অনেক অনলাইন পোর্টাল খবর প্রকাশ করে, যার পরপরই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং দাঙ্গার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। অথচ সাংবাদিকরা যদি সময় নিয়ে যাচাই করতেন, তাহলে বোঝা যেত পোস্টটি ভুয়া আইডি থেকে করা হয়েছিল।
শুধু বাংলাদেশ নয়, আন্তর্জাতিক পরিসরেও এই প্রবণতা ভয়াবহ প্রভাব ফেলেছে। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সংকট চলাকালে অসংখ্য ভুয়া ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। অনেক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম যাচাই ছাড়া সেগুলো ব্যবহার করে। পরে প্রমাণিত হয় ছবির কিছু আসলে আফ্রিকা মহাদেশের, আবার কিছু ছিল বহু বছর আগের। এই ধরনের ভুল শুধু পাঠককে বিভ্রান্ত করেনি, বরং সাংবাদিকতার প্রতি মানুষের আস্থাকে মারাত্মকভাবে নষ্ট করেছে। একইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের সময় কিংবা ব্রেক্সিট গণভোটে ভুয়া খবর ব্যাপকভাবে সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে ছড়িয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময়ও দেখা গেছে, অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ভুয়া খবর ও গুজব মানুষের আতঙ্ক বাড়িয়েছে, ভ্যাকসিন নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে এবং স্বাস্থ্যনীতি কার্যকরে সমস্যা সৃষ্টি করেছে।
প্রশ্ন হলো, কেন সাংবাদিকরা সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্য যাচাই না করেই ব্যবহার করছেন? এর পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে দ্রুততার প্রতিযোগিতা। কে আগে খবর প্রকাশ করবে, এই দৌড়ে যাচাই-বাছাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অনেক সময় বাদ পড়ে যায়। দ্বিতীয়ত, সাংবাদিকদের উপর প্রচণ্ড চাপ কাজ করে। অনলাইন নিউজ পোর্টাল সারাক্ষণ আপডেট দিতে চায়, ফলে সাংবাদিকরা অনেক সময় সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টকে সংবাদ হিসেবে ছাপতে বাধ্য হন। তৃতীয়ত, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও রিসোর্সের অভাব। অনেক সাংবাদিক জানেন না কীভাবে কোনো ছবি বা ভিডিওর সত্যতা যাচাই করতে হয়। অথচ গুগল রিভার্স ইমেজ সার্চ, ইনভিড কিংবা নানা ফ্যাক্ট-চেকিং টুল ব্যবহার করে সহজেই বোঝা যায় কোনো ছবি পুরোনো নাকি বিভ্রান্তিকর। এর পাশাপাশি অনলাইন মিডিয়ার ক্লিকবেইট সংস্কৃতিও দায়ী। পাঠকের দৃষ্টি
আকর্ষণ করতে অনেক সময় অনলাইন পোর্টালগুলো উসকানিমূলক শিরোনাম দিয়ে সংবাদ ছাপে, যেখানে
তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত না হয়েও খবর প্রকাশ করা হয়।
এই প্রবণতার কারণে সাংবাদিকতার মান ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পাঠক ধীরে ধীরে সংবাদপত্রের
প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন। যখন তারা দেখেন, কোনো গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভুয়া বলে প্রমাণিত হচ্ছে, তখন তারা আর সেই গণমাধ্যমের উপর ভরসা রাখতে চান না। এর ফলে ভুয়া খবর ও গুজব আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষ তখন সরাসরি সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্য বিশ্বাস করতে শুরু করেন, অথচ সেখানেই সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তি তৈরি হয়। একবার মানুষের মনে সংবাদপত্রের প্রতি অবিশ্বাস জন্মালে সেই আস্থা পুনরুদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।
তবে সমাধানের পথও আছে। সাংবাদিকদের এবং গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদের ভূমিকা পুনর্র্নিধারণ করতে হবে। সংবাদ প্রকাশের আগে যাচাই নিশ্চিত করতে আলাদা ফ্যাক্ট-চেকিং টিম গঠন করা জরুরি, যারা ছবি, ভিডিও এবং তথ্যের উৎস নির্ভুলভাবে যাচাই করবে। সাংবাদিকদের প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যাতে তারা রিভার্স ইমেজ সার্চ কিংবা ভুয়া ভিডিও শনাক্তকরণ টুল ব্যবহার করতে পারেন। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে কঠোর নীতি গ্রহণ করতে হবে যাতে যাচাই ছাড়া কোনো তথ্য প্রচার করা না যায়। একইসঙ্গে সাংবাদিকতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং ভুয়া তথ্য শনাক্তকরণ কৌশল পড়ানো প্রয়োজন।
এখানে এটিও মনে রাখতে হবে যে সোশ্যাল মিডিয়া পুরোপুরি নেতিবাচক নয়। এটি অনেক সময় সাংবাদিকদের জন্য প্রাথমিক সূত্র হিসেবেও কাজ করে। কোনো দুর্ঘটনা বা ঘটনার খবর প্রথমে সোশ্যাল মিডিয়াতেই প্রকাশিত হয়। সাংবাদিকরা চাইলে সেই সূত্র ধরে প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে কথা বলতে পারেন, মাঠপর্যায়ে অনুসন্ধান করতে পারেন এবং আসল সত্য উদঘাটন করতে পারেন। সমস্যা তৈরি হয় তখনই, যখন যাচাই প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে সরাসরি সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্যকেই খবর হিসেবে গ্রহণ করা হয়।
ভবিষ্যতে সাংবাদিকতার জন্য আরও বড় চ্যালেঞ্জ আসছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে তৈরি
“ডিপফেইক” প্রযুক্তি ইতোমধ্যেই মানুষকে বিভ্রান্ত করতে শুরু করেছে। ভুয়া ভিডিও বা অডিও সহজেই তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে, যেগুলো সাধারণ পাঠকের পক্ষে আসল নাকি ভুয়া তা বোঝা কঠিন। সাংবাদিকদের তাই আরও দক্ষ হতে হবে এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সত্য যাচাই করতে হবে। নাহলে ভবিষ্যতে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়তে পারে।
গণতান্ত্রিক সমাজে সংবাদপত্র শুধু তথ্য সরবরাহ করে না, বরং মানুষের আস্থা ও নিরাপত্তার অনুভূতি
জাগায়। সংবাদপত্রের দায়িত্ব হলো সত্য প্রকাশ করা, মানুষের মধ্যে সঠিক সচেতনতা তৈরি করা। যদি
সংবাদপত্রই ভুয়া তথ্য ছড়ানোর উৎসে পরিণত হয়, তবে সেই আস্থা ভেঙে যাবে। তাই দ্রæততার চেয়ে
নির্ভরযোগ্যতাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। পাঠক যদি নিশ্চিত হতে পারেন যে কোনো পত্রিকার খবর যাচাইকৃত ও সত্য, তখনই তারা সেই গণমাধ্যমকে মর্যাদা দেবেন।
অতএব, সাংবাদিকতা আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে সোশ্যাল মিডিয়ার দ্রুততা, জনপ্রিয়তা ও প্রভাব, অন্যদিকে সংবাদপত্রের ঐতিহ্য, দায়িত্ব ও বিশ্বাসযোগ্যতা। এই দুইয়ের মধ্যে সঠিক সমন্বয় করতে না পারলে সাংবাদিকতার মান দিন দিন নিম্নগামী হবে। এখনই সময় সাংবাদিকদের পেশাদারিত্বে ফিরে আসার, সোশ্যাল মিডিয়াকে তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করার, কিন্তু যাচাই ছাড়া কোনো তথ্য সংবাদ হিসেবে গ্রহণ না করার। কেবল তখনই গণমাধ্যম সমাজের আস্থা পুনরুদ্ধার করতে পারবে এবং সত্যের আলোয় আলোকিত করতে পারবে পুরো সমাজকে।
লেখক পরিচিতিঃ
ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক।

