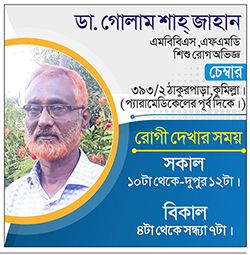ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চায় না!
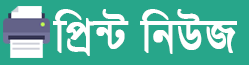
মনোয়ার হোসেন রতন।।
এই শিরোনাম দিয়েছি একেবারেই সচেতনভাবে। কারণ, ভারতের রাজনৈতিক নীতি কখনোই বাংলাদেশের প্রতি খাঁটি বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না—ছিল কৌশলী অভিনয় মাত্র। ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব, আঞ্চলিক আধিপত্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থের খেলায় ভারত বরাবরই নিজেদের লাভকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, আর বাংলাদেশকে সেই স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।
আমার বাবা জন্মেছিলেন ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে, তখন ছিল ব্রিটিশ ভারত। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা চলে গেলে জন্ম নিল ভারত ও পাকিস্তান—আমার বাবার জীবনে প্রথমবার মানচিত্র পরিবর্তন হলো। এরপর ১৯৭১—পাকিস্তান ভেঙে জন্ম নিল বাংলাদেশ, আমরা পেলাম একটি নতুন পতাকা, একটি নতুন রাষ্ট্র, কিন্তু পেলাম নতুন কৌশলী শক্তির নজরদারি ও প্রভাবও।
ইতিহাস বলে—যে রাষ্ট্রের জন্মে বিদেশি শক্তির কৌশলগত স্বার্থ জড়িয়ে থাকে, সেই রাষ্ট্রকে কখনোই পুরোপুরি স্বাধীন থাকতে দেওয়া হয় না। মুক্তিযুদ্ধে ভারত আমাদের সহায়তা করেছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সহায়তা নিছক মানবিকতার কারণে ছিল না—ছিল তিনটি বড় কৌশলগত লক্ষ্য পূরণের পরিকল্পনা:
১. পূর্ব সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা—পাকিস্তানের দুই দিকের চাপ থেকে মুক্তি।
২. বাংলাদেশকে ভারতের অর্থনৈতিক বাজারে পরিণত করা—আমাদের পণ্য আমদানির চেয়ে তাদের রপ্তানি বাড়ানো।
৩. রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার—যাতে বাংলাদেশ ভারতের কূটনৈতিক অবস্থানকে সমর্থন করে।
মুক্তিযুদ্ধের পরপরই এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হয়। ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে গঙ্গার পানি সরিয়ে নেওয়া, সীমান্ত হত্যা, অসম বাণিজ্য চুক্তি—সবই এর অংশ। আজ পর্যন্ত পানির ন্যায্য হিস্যা আমরা পাই না। ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানির ভাগ ভারত নিজের মতো নিয়ন্ত্রণ করে।
রাজনীতির ক্ষেত্রেও ভারতের ছায়া স্পষ্ট। যে সরকার ভারতের অনুগত, ভারত তাকে টিকিয়ে রাখতে সর্বশক্তি ব্যবহার করে। ২০০৮ সালের নির্বাচন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যন্ত—ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতা ও গোপন সমর্থন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার সমীকরণ বদলে দিয়েছে। এতে বাংলাদেশের গণতন্ত্র দুর্বল হয়েছে, আর ক্ষমতার রাজনীতি নির্ভরশীল হয়েছে দিল্লির আশীর্বাদের উপর।
অর্থনীতিতেও ভারতের প্রভাব ভয়ঙ্কর। আমাদের বাজারে ভারতীয় পণ্যের একচেটিয়া আধিপত্য, আর আমাদের শিল্পপণ্য রপ্তানিতে নানা অজুহাতে বাধা। ট্রানজিট সুবিধা, বিদ্যুৎ আমদানি, রেল ও সড়ক সংযোগের নামে ভারতের পণ্য ও জ্বালানি পরিবহনের পথ খুলে দেওয়া হয়েছে—যার সুবিধা ভারতের, চাপ বাংলাদেশের।
কৌশলগত দিক থেকেও ভারতের আগ্রহ স্পষ্ট—চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার, স্যাটেলাইট তথ্য বিনিময়, সীমান্ত নজরদারি—সবই বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানকে ভারতের সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগানোর প্রক্রিয়া। অথচ পাল্টা আমরা পাই সীমিত সুবিধা, আর নির্ভরশীলতা বেড়ে যায় বহুগুণ।
ইতিহাসের পর্যালোচনা স্পষ্ট করে বলে—যে জাতি নিজের সম্পদ, পানি, সীমান্ত, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না, সেই জাতির স্বাধীনতা কেবল নামমাত্র থাকে। আজ আমরা পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে আছি ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে আমাদের স্বাধীনতা শর্ত, চাপ ও চুক্তির শৃঙ্খলে বাঁধা।
বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানের শোষণ থেকে মুক্তি পেয়েছিল, কিন্তু যদি ভারতের আধিপত্যে আবদ্ধ হয়, তাহলে আমাদের স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ কোথায়? পাকিস্তান আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে দমিয়ে রাখতে চেয়েছিল, আজ ভারতের নীতি ঠিক একই রকম—শুধু পদ্ধতি ভিন্ন।
প্রশ্ন হলো—আমরা কি আবারও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির দিকে এগোচ্ছি? মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল প্রকৃত স্বাধীনতা, কেবল ভৌগোলিক সীমারেখা নয়। স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে শত্রুকে শুধু সীমান্তের বাইরে নয়, সীমান্তের ভেতর থেকেও চিনতে হবে।
বাংলাদেশকে টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদের তিনটি কাজ জরুরি—
১. অর্থনীতিতে স্বনির্ভরতা অর্জন।
২. পানির ও সম্পদের ন্যায্য হিস্যা আদায়।
৩. অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে বিদেশি প্রভাবমুক্ত করা।
আমরা যদি এই কাজগুলো করতে ব্যর্থ হই, তবে হয়তো কয়েক দশক পর ইতিহাস বইয়ে লেখা থাকবে—”বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্র ছিল, কিন্তু সেটি সত্যিকার অর্থে স্বাধীন ছিল না।”