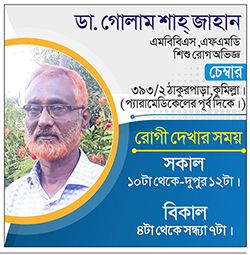ষড়যন্ত্রের ঘূর্ণি ও ইতিহাসের মাঝপথে ড. ইউনূস
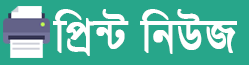
মনোয়ার হোসেন রতন।।

২০২৪ সালের বর্ষাকাল ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণ। রাজপথে তরুণ সমাজের গর্জন, পতনমুখী একদলীয় শাসনের অবসান এবং নতুন সূর্যোদয়ের প্রত্যাশা—সব মিলিয়ে দেশ যেন প্রবেশ করেছিল এক অভাবনীয় মোড়ের মধ্যে।
এই মোড়ে দাঁড়িয়ে জাতি প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, এবং নৈতিক শক্তির প্রতীক একজন মানুষকে পেয়েছিল—নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
তিনি কোনো দলে ছিলেন না, ছিলেন জনতার পক্ষের এক বিবেক, এক নির্মোহ পথপ্রদর্শক। তাঁর কথায় ছিল সত্যের স্বর, চাহনিতে ভবিষ্যতের স্পষ্ট রেখাচিত্র। এমন মানুষ যখন রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রে আসেন, তখন স্বপ্ন দেখা মানে আর শুধু কল্পনা থাকে না—তা হয়ে ওঠে সম্ভাবনার বাস্তব পথরেখা।
আলোকবর্তিকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ছায়া
ড. ইউনূস দায়িত্ব নেন ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে, দেশের অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান হিসেবে। দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেন—“বাংলাদেশের সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় রয়েছে।” তাঁর এই তীক্ষ্ণ উচ্চারণ ছিল না কোনো প্রতিশোধস্পৃহা থেকে; বরং তা ছিল নিষ্ঠুর বাস্তবতার নগ্ন স্বীকৃতি।
তিনি শুরু করলেন এক শুদ্ধিকরণের যাত্রা।
- সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনশুনানি চালু করা হলো,
- দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহের জন্য খোলা হলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের “জনদর্পণ” ইউনিট,
- গঠিত হলো “Consensus Commission”,
- এবং সর্বোপরি—৩০টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐকমত্য তৈরির জন্য “July Charter” খসড়া তৈরি হয়।
এই সংস্কারমূলক কার্যক্রমগুলোর মধ্য দিয়ে ইউনূস দেখিয়েছিলেন—রাষ্ট্র মানে কেবল শাসনের কেন্দ্র নয়, বরং ন্যায় ও স্বপ্নের বিস্তার।
কিন্তু যেখানেই সত্য দাঁড়ায়, সেখানেই জন্ম নেয় প্রতিরোধ
ড. ইউনূসের বিপরীতে প্রতিক্রিয়া এসেছিল চারটি স্তরে—
প্রথমত, রাজনৈতিক পরিবারতন্ত্র আতঙ্কিত হয়ে ওঠে।
যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ক্ষমতার অলিন্দে অভ্যস্ত, তারা ইউনূসকে দেখল এক অস্বস্তিকর ‘বহিরাগত’ হিসেবে। তিনি ছিলেন এমন একজন—যার মধ্যে ছিল না চাটুকারিতা, ছিল না দলে-গোষ্ঠীতে জড়িয়ে থাকার ইতিহাস।
ফলে তাঁর বিরুদ্ধে গড়ে উঠল অপপ্রচারের এক সুসংগঠিত মঞ্চ, যেখানে তাঁকে কখনো বলা হলো ‘অরাজনৈতিক স্বৈরাচার’, আবার কখনো ‘বিদেশি এজেন্ডার বাহক’।
দ্বিতীয়ত, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল শঙ্কামূলক।
শেখ হাসিনার সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছিল উষ্ণ ও সুবিধাজনক। কিন্তু ইউনূসের নেতৃত্ব ছিল স্বতন্ত্র ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ। ভারত যখন দেখল এই নেতৃত্ব কারও ‘মিত্র’ নয়, বরং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ স্বার্থে আপসহীন—তখনই শুরু হলো কূটনৈতিক দূরত্ব ও নীরব চাপ।
তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেখানে তাঁর সংস্কারকে স্বাগত জানায়, সেখানে চীন ও রাশিয়া অবস্থান নেয় নিরপেক্ষ বা নিস্পৃহ ভূমিকায়। এই অসম আন্তর্জাতিক পরিবেশ ইউনূসের কাঁধে আরও ভারী দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়।
চতুর্থত, বিরোধী রাজনীতির দ্বৈত মুখোশ।
সব বিরোধী শক্তি প্রথমে ইউনূসের আগমনকে স্বাগত জানালেও, পরে তারা বুঝতে পারে—এই মানুষটির উপস্থিতিতে তাদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সুবিধা হুমকির মুখে পড়বে।
ফলে শুরু হয় সন্দেহের রাজনীতি, সহযোগিতার আড়ালে কূটনৈতিক ভঙ্গিমা।
তিনি কি কেবল ক্ষমতাধর এক ব্যক্তি ছিলেন?
না। ড. ইউনূস ছিলেন সমাজ রূপান্তরের এক নির্লোভ কারিগর।
যেমন তিনি ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে অর্থনীতিকে মানুষের ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তেমনই অন্তর্বর্তী সময়কালে প্রশাসনকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন জনতার দরবারে।
তিনি বিশ্বাস করতেন—রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দায়িত্ব জনগণের কাছে জবাবদিহিতার মধ্যেই নিহিত।
তাই তিনি শুধু নির্বাচনের প্রস্তুতি নেননি, নিয়েছেন জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব।
তিনি ঘোষণা করেছিলেন:
“আমি ক্ষমতা চাই না, চাই দেশের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য, স্বচ্ছ নির্বাচন।”
এক সাক্ষাৎকার, এক নিঃশব্দ আহ্বান
২০২৫ সালের ১২ জুন, ‘দ্য গার্ডিয়ান’-এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ড. ইউনূস বলেন:
“আজও মানুষ সরকারকে দেখে শত্রু হিসেবে। আমি দায়িত্ব নিতে চাইনি, দেশের ডাকেই এসেছি।”
এই কথাগুলি শুধু একজন মানুষের বেদনামথিত আত্মপ্রকাশ নয়, বরং বাংলাদেশের বাস্তবতার এক নির্মম প্রতিবিম্ব।
তাঁকে সফল হতে দেওয়া হয়নি—তবু তিনি ব্যর্থ নন
প্রতিপক্ষেরা তাঁকে রুখে দিতে চেয়েছে, তাঁর আদর্শকে ঘোলাটে করতে চেয়েছে, ইতিহাসকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে।
কিন্তু তিনি মাথা নত করেননি, আপস করেননি, পিছু হটেননি।
তাঁর হাতে গড়ে উঠেছিল এমন এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, যা জনগণের অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা এবং সংলাপের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার নতুন ভাষ্য রচনা করেছিল।
ইতিহাস চুপ থাকে, তবে বিস্মৃত হয় না…
একদিন এ জাতি বুঝবে, ২০২৪-২৫ সালে সত্যিই একবার আলো জ্বলে উঠেছিল বাংলার ঘরে। সেই আলো ছিল ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
তিনি হয়তো চূড়ান্ত বিজয়ী নন, কিন্তু তিনি পরাজিতও নন। কারণ যিনি স্বপ্ন দেখাতে পারেন, সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, আর ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে পারেন—তাঁকে ইতিহাস মুছে ফেলতে পারে না।
তাঁকে ভাঙার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তিনি ভাঙেননি। কারণ ইতিহাসের সত্য কখনো ভাঙে না—শুধু সময়মতো জেগে ওঠে, দীপ্ত হয়ে ওঠে।