কলের গান ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
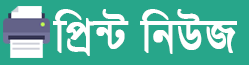
।। আবদুল আজিজ মাসুদ ।।
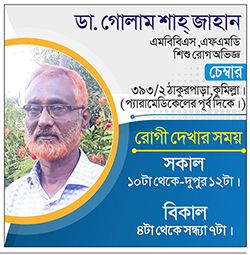

অনেকেই বলে পুরনো রেকর্ড বাজিয়ে লাভ নেই। আমি বলি! লাভ আছে, যদি পুরনো রেকর্ড এখনো বাজে, না বাজলেও মন্দ কি! এন্টিক লাভারদের কাছে তো মহামূল্যবান সম্পদ।
সেদিন জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে “কলের গান, সে কাল এ কাল” শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম। থরেথরে সাজানো বৃটিশ আমলের হিজ মাস্টার্স ভয়েজ গ্রামোফোন কোম্পানির চোঙ্গা বা এক্সটারনাল হর্ন এর সামনে বসা কুকুরের ট্রেডমার্ক ওয়ালা গ্রামোফোন মেশিন, রেকর্ড। দেখে মনে হয়েছিল “অচল যন্ত্র”, কিন্তু না গ্রামোফোন মেশিনের হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে স্প্রিংয়ে দম দিলেই সচল। ঘুরতে থাকা রেকর্ডে, বাঁকানো হাতলের মাথায় লাগনো পিন স্পর্শ করালেই বেজে উঠে সেকালের বিখ্যাত শিল্পীদের কন্ঠে কালজয়ী গান, এদের মধ্যে নজরুল সঙ্গীতশিল্পী হরিমাত, ইন্দুবালা, কাননবালা, আঙ্গুরবালা, আব্বাস উদ্দিন, কমলদাশ গুপ্ত, শচীন দেব বর্মনসহ আরো বিখ্যাত শিল্পীদের গান। ত্রিশ/চল্লিশের দশকে জাতীয় কবি নজরুল ছিলেন হিজ মাস্টার্স ভয়েজ গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গীত ট্রেনার। নজরুল গান রচনা ও সুর করে শিল্পীর কন্ঠে তুলে দিতেন।
সুকন্ঠী, অভিনেত্রী, নৃত্যশিল্পী হরিমতির কন্ঠে নজরুলের “ঝরা ফুল দলে কে অতিথি/সাঝের বেলা এলে কাননবীথি’ অথবা “কে নিবি ফুল, কে নিবি ফুল / চামেলি যুথী বেলী, মালতি / চাঁপা গোলাপ বকুল” কার না শুনতে ভালো লাগে। কানন বালার অনবদ্য কন্ঠে “ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে আমি বন ফুলগো” অথবা নজরুলের “আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই” এ সমস্ত গান ত্রিশ/চল্লিশের দশকে ছিল ঢাকা কলকাতাবাসীর মুখে মুখে।
প্রদর্শনীতে শিল্পী সম্পর্কে বিভিন্ন পোস্টার, ক্যাপশনে উল্লেখ আছে “বাঈজী ও বারাঙ্গনাদের সামাজিক ভাবে যতই অপাক্তেয় করে রাখা হোক না কেন, এরাই সে সময় মানুষকে দিয়ে ছিল আনন্দ বিনোদনের মূল খোরাক। সঙ্গীত, নৃত্যসহ শিল্পকলার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শাখার বিকাশে তাদের অবদান ছিল অভূতপূর্ব, তাদের গড়া পথেই পরবর্তী সময়ে শিক্ষিত পরিবারের মেয়েরা স্বচ্ছন্দে সাংস্কৃতি অঙ্গনে পা ফেলতে পেরেছিল্ কিন্তু তাদের অবদানের কথা এখন বিস্মৃত প্রায়, এমনকি তাদের নামই হারিয়ে গেছে।” অভিনেত্রী কাননবালা দেবী (১৯১৬-১৯৯২) তাঁর স্মৃতি কথায় বলেন, “আমি মানুষ সেই পরিচয় টাই আমার কাছে যথেষ্ঠ।” “অন্ধকারে জন্মেও তারা আলোর দিশারী, বাঈজী থেকে দেবী হতে পেরেছিলেন তারা সঙ্গীতকেই সঙ্গী করে। আর সেই পথটি ছিল বরাবরই চোখের জলে সিক্ত।” ত্রিশের দশকের নামকরা বাঈজী সুকন্ঠী হরিমতি ঢাকার প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র (১৯৩১) “দি লাস্ট কিস” এ অভিনয় করেছিলেন। হরিমতি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবে বিধবা হয়ে ঢাকায় চলে আসেন পরে আবার কলকাতায় ফিরে যান। হরিমতির ছোট বোন বাঈজী রাজবালার মেয়ে বিখ্যাত ইন্দুবালা (১৮৯৮-১৯৮৪)।
সেকালের কলিকাতার যৌনাচার গ্রন্থে মানস ভান্ডারী ইন্দুবালা সম্পর্কে লিখেন, “তাঁর মা দিদিমা ছিলেন রামবাগানের পতিতা। অন্ধকারের জীবনে তিনিও প্রথমে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে খ্যাতি ও উজ্জলতায় উদ্ভাসিত হলেও তিনি কখনো কোথাও নিজের পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করেননি। পতিতা পল্লীতে তাদের তিন পুরুষের বসবাস। সেই জায়গায় তিনি মৃত্যু পর্যন্ত বসবাস করতে চেয়েছেন।” তিনি অন্যত্র বলেছেন “পাড়া বদলে নামের শেষে ‘বালা’ বাদ দিয়ে আমি দেবী হতে পারব না”। ইন্দুবালা বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, উর্দু, তামিল ভাষায় গান গেয়ে দেশ বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনশ’র বেশি রেকর্ড। মুম্বাই-চেন্নাই গিয়ে চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত ছবির সংখ্যা ৫০। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের লেখা গল্প নিয়ে One Fatal Night নামে ১৯৩৬ সনে নির্মিত উর্দু ছবিতে অভিনয় করেন। ১৯২৬ সালে কলকাতা রেডিও’র উদ্বোধনের দ্বিতীয় দিনে গান করেন। শুধু নজরুলেরই লেখা ৪৮টি গান রেকর্ড করেছেন। নজরুল ইন্দুবালাকে আদর করে “নানি” বলে ডাকতেন। কৃষ্ণ চন্দ্র দে এবং নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সম্মান, প্রতিষ্ঠা, মেডেল, সংবর্ধনা পেয়েছেন প্রচুর। তার রেকর্ডের গান শুনেছেন রবীন্দ্রনাথ।”
আগেই বলেছি সে কালে অর্থাৎ মোগল বৃটিশ যুগে যখন রঙ্গমঞ্চে নারী চরিত্র নিষিদ্ধ বা সংকট ছিল তখন এই বাঈজী বারাঙ্গনাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অনুপ্রবেশে চলচ্চিত্র, রঙ্গমঞ্চে ব্যাপক আলোড়ন ও আলোচনা-সমালোচনার সূত্রপাত ঘটায়! সেকালে নাটকে পুরুষরাই নারী চরিত্রে অভিয়ন করতেন।
১৮৭৩ সালে বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হলে মধুসূদন দত্তের “শার্মিষ্ঠা” নাটকে নিষিদ্ধ পল্লীর সুকুমারী দত্ত বা গোলাপ সুন্দরী অভিনয় করে প্রশংসা কুড়ান। পরে মেঘনাথ বধ কাব্য (১৮৭৭) সহ অন্যান্য নাটকে এই নিষিদ্ধ পল্লীর নারীরাই অভিনয় করেন। সেকালের ঢাকা ছিল নাচ গানে ভরপুর। নিজস্ব বাগানবাড়ি বা নাচমহলে বাঈজী নৃত্য ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। সুবেদার ইসলাম খাঁ’র দরবারে প্রায়ই মেহফিল বা নাচগানের আসর বসতো। তাঁর দরবারে বারোশ’ কাঞ্জনী অর্থাৎ নর্তকী ছিল। তাঁদের পেশা ছিল নাচগান করা। ঢাকা ছিল সঙ্গীত ও তালের শহর। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঈজীদের নাচগানের উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষ লাভ করে। বাঈজীরা প্রায়ই তখন আহসান মঞ্জিল, শাহ্বাগের ইশরাত মঞ্জিল, দিলকুশার বাগান বাড়িতে নাচগানের মেহফিলে অংশ নিতেন। বিখ্যাত গহরজান, মলাকা জান, বেগম আখতার, জদ্দন বাঈ, মুসতারী বাঈ, কলকাতা থেকে ঢাকার মেহফিলে অংশ নিয়েছিল।
মালকাজান, গহরজান সম্পর্কে জানা যায় গহরজান ১৮৬৩ সালে প্রথম কলকাতায় আসেন হায়দারাবাদের নিজামের পৃষ্ঠপোষকতায়। তিনি মহীশূর রাজদরবারেও সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। তিনি ইন্ডিয়ান নাইটেঙ্গল উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর মা মালকাজানও বিখ্যাত বাঈজি ছিলেন এবং কবি ও গীতিকার ছিলেন। তারা দুজনেই খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।
সে দিনের বিশেষ প্রদর্শনীতে ষাট-সত্তর দশকের সেই সোনালী যুগের চলচ্চিত্রের গানের অংশ বিশেষ প্রদর্শনী দর্শক স্রোতাদের মুগ্ধ করেছে। এগুলোর মধ্যে ছিল, “রংবাজ, মনের মানুষ, সুতরাং, রূপবান, অবুঝ মন, ময়নামতি, সাহেব” ইত্যাদি সিনেমার গান। প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে ষাটের দশকে ঢাকার ব্যান্ড সংগীতের সূচনার ইতিহাস। ষাটের দশকে নাজমা জামান জিংগা শিল্পী গোষ্ঠী ঢাকায় ব্যান্ড সংগীতের সূচনা করেন। ইএমআই রেকর্ড কোম্পানি ১৯৬৯ সালে জিংগা গোষ্ঠীর প্রথম রেকর্ড বের করে। “উইন্ডি সাইড অব কেয়ার” ব্যান্ড সংগীত শিল্পী গোষ্ঠী ১৯৬৫ সনে শাহ্বাগ হোটেল, ঢাকা ক্লাব ও হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নিয়মিত পারফর্ম শুরু করে। তখন এই দল ছিল তরুণদের ক্রেজ। তারাই প্রথম ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে দর্শনীর বিনিময়ে কনসার্টের আয়োজন করে। ইএমআই রেকর্ড কোম্পানি তাদের একটি রেকর্ড বের করে।
লেখক:
আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
মোবাইল: ০১৭১১-৪৬৪২১৩
ইমেইল: [email protected]

